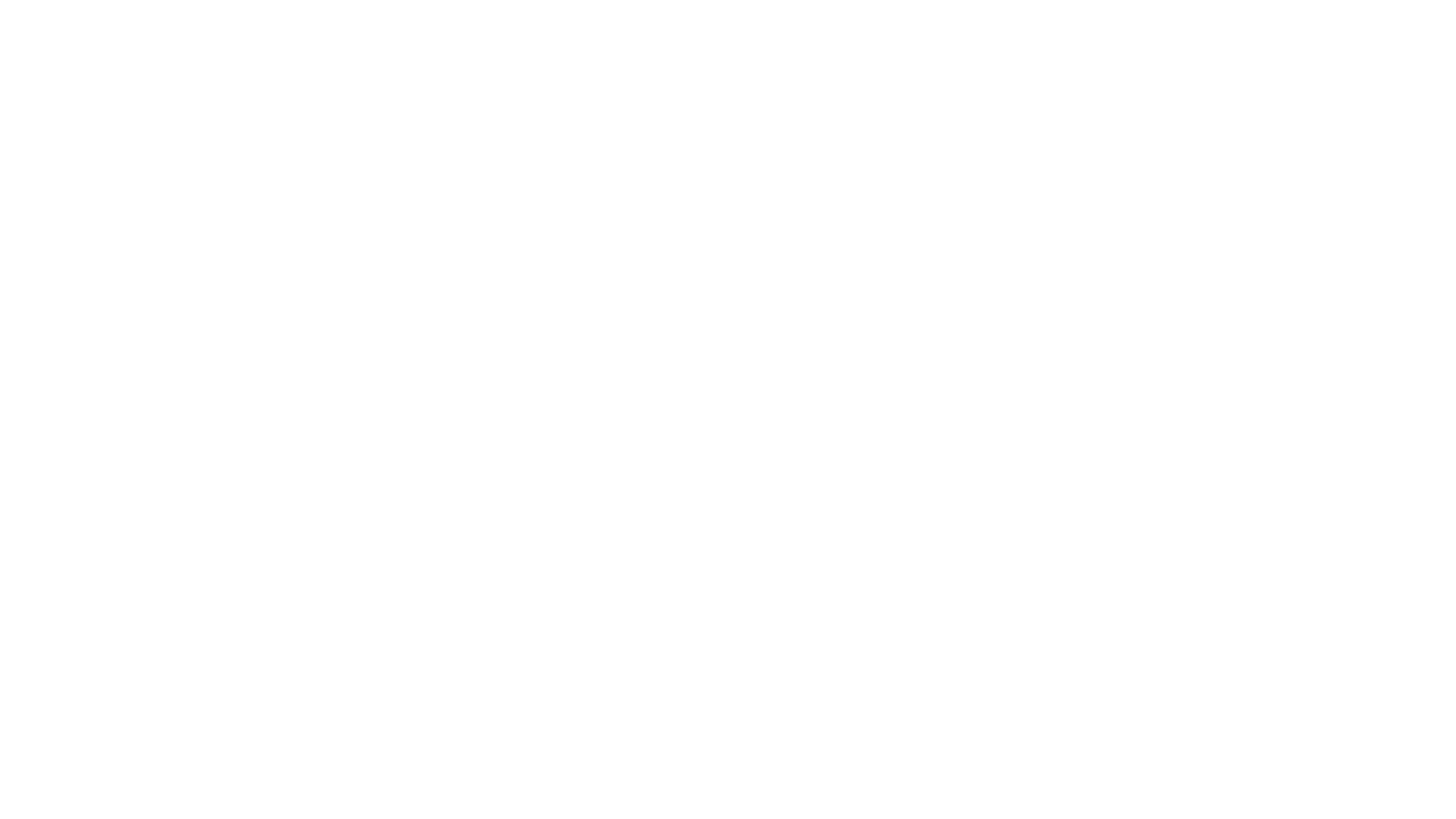মহাশ্বেতা দেবী: প্রতিবাদের এক অপরাজেয় মুখ

মহাশ্বেতা দেবী ইতিহাস থেকে, রাজনীতি থেকে যে সাহিত্য রচনা শুরু করেন, তা শোষিতের আখ্যান নয় বরং স্বদেশীয় প্রতিবাদী চরিত্রের সন্নিবেশ। তিনি প্রতিবাদী জীবন ও সাহিত্যের এক স্বতন্ত্র ঘরানার লেখিকা। সামাজিক দায়বোধ থেকেই তিনি তাঁর সেই উপেক্ষিত ইতিহাসের নায়কদের তুলতেন।
মহাশ্বেতা দেবী আজীবন সংগ্রামী চিন্তা চর্চা করেছেন এবং দেশ ও মানুষ সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত হবে সেই লক্ষ্যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সক্রিয় কর্মী, তাঁর সংগ্রাম চলেছে সাহিত্যচর্চা এবং জীবনচর্চার মাধ্যমে। পারিবারিকভাবেই তিনি এক সাহিত্যবেষ্টিত পরিমণ্ডলে বড় হয়েছেন এবং সাহিত্যকেই জীবনে বেছে নিয়েছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে দু’টি কবিতা উপহার দিয়েছিল।
১৯৩৬ সালে তিনি পড়াশোনা করতে শান্তিনিকেতনে যান। তখনই তাঁর লেখালেখির শুরু। ১৯৩৯ সালে তিনি যখন অস্টম শ্রেণীতে পড়েন, তখন খগেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত ‘রংমশাল’ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত রচনা ‘ছেলেবেলা’।
১৯৪৩-এ পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময় মহাশ্বেতা দেবী প্রথম বর্ষে পড়াকালীন কম্যুনিস্ট পার্টির ছাত্রী সংগঠন ‘Girls’ Student Association এবং ত্রাণের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কম্যুনিস্ট পার্টির মিটিংয়ে যোগ দিতেন, পার্টির মুখপত্র ‘People’s War’, ‘জনযুদ্ধ’ বিক্রী করতেন এবং সে পত্রিকার নিয়মিত পাঠকও ছিলেন। তবে পার্টির মেম্বার না হয়ে এভাবেই কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মূলত তখন থেকেই তাঁর কর্মীসত্তার বিকাশ, যা পরবর্তীকালে তাঁর জীবনে আরও প্রকট হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ সালে বিশিষ্ট নাট্যকার এবং কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাদের সংসার জীবন ছিল দারিদ্র্যে পরিবেষ্টিত—এ সময় মহাশ্বেতা দেবী রঙ সাবান, রঙের গুঁড়ো ফেরি করেন, ছাত্র পড়ানো শুরু করেন। ১৯৪৮ সালে তাঁর একমাত্র পুত্র নবারুণ ভট্টাচার্য়ের জন্ম হয়। তাদের সংসার জীবন পনের বছরের বেশী টেঁকেনি।
তিনি সুমিত্রা দেবী ছদ্মনামে ‘সচিত্র ভারত’ পত্রিকায় ফিচার এবং গল্প লেখা শুরু করেন। যদিও ১৯৪৯ সালে ইনকাম ট্যাক্সে কেরানির চাকরি পান, কিন্তু সে চাকরি তাঁর করা হয়ে ওঠে না। এরপর তিনি কেন্দ্রীয় সরকারে পোস্টাল অডিটে আপার ডিভিশন ক্লার্কের চাকরি নেন। কিন্তু সেখানে রাজনৈতিক সন্দেহে চাকরি থেকে বরখাস্ত হন, পরবর্তীকালে পুনর্বার চাকরিতে বহাল হলেও তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে সরকারি চাকরিতে ফেরেন নি।
দীর্ঘ পড়াশোনা বিরতির পর ১৯৬৩ সালে তিনি প্রাইভেটে ইংরেজিতে এম. এ পাশ করেন এবং ১৯৬৪ সালে তিনি ইংরেজি অধ্যাপনায় প্রবেশ করেন বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজে। ইতোমধ্যে তাঁর প্রথম বই ঝাঁসীর রানী (১৯৫৬) প্রকাশ পায়। পরবর্তীতে তিনি লেখাকেই পেশা হিশেবে গ্রহণ করেন।
ইতিহাস তাঁর সাহিত্যজীবনে সব সময়ই গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। তিনি মনে করতেন ইতিহাসের মুখ্য কাজই হচ্ছে একই সঙ্গে বাইরের গোলমাল, সংগ্রাম ও সমারোহের আবর্জনা এবং ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে জনবৃত্তকে অন্বেষণ করা, অর্থ ও তাৎপর্য দেওয়া। এর মাধ্যমে বেরিয়ে আসবে সমাজনীতি ও অর্থনীতি, যার মানেই হলো লোকাচার, লোকসংস্কৃতি, লৌকিক জীবনব্যবস্থা।
তিনি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় খুদাবক্স ও মোতির প্রেমের কাহিনী নিয়ে ১৯৫৬ সালে নটী উপন্যাসটি লিখেন। এছাড়া প্রথম পর্যায়ে তিনি লোকায়ত নৃত্য-সংগীতশিল্পীদের নিয়ে লিখেছেন মধুরে মধুর (১৯৫৮), সার্কাসের শিল্পীদের বৈচিত্র্যময় জীবন নিয়ে লিখেন প্রেমতারা (১৯৫৯)। এছাড়া যমুনা কী তীর (১৯৫৮), তিমির লগন (১৯৫৯), রূপরাখা (১৯৬০), বায়োস্কোপের বাক্স (১৯৬৪) প্রভৃতি উপন্যাস। মহাশ্বেতা দেবী নিজের লেখা সম্পর্কে নিজেই সমালোচক হয়ে উঠেছেন কখনও কখনও। ইতিহাসচর্চা আর সমাজ-সচেতনতায় দৃঢ় হয়ে উঠেন বলেই যেন তাঁর প্রথম পর্বের দুটো উপন্যাস তিমিরলগন ও রূপরাখা-তে ব্যক্তির সুখ-দুঃখ যখন কোনো সামাজিক তাৎপর্য বহন করে না বলে মনে করেছেন, তখন তিনি এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেন—ওই বই দুটো আর ছাপবেন না। আবার অন্যদিকে গভীর সামাজিক তাৎপর্য থাকার জন্য, প্রথম প্রকাশের কুড়ি বছর পরেও ‘বিষয়বস্তুর চিরকালীনতা ও প্রয়োজনীয়তা আজও’ রয়েছে বলে মহাশ্বেতা দেবী মনে করেন, ‘মধুরে মধুর’…আজকের পাঠকের কাছে বইটি থাকা দরকার। দু-অর্থে। আমার লেখার বিবর্তনের সাক্ষ্যে এবং ব্যক্তি সংগ্রামের যাথার্থ্যে।’
১৯৬২ সালে বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। সংসার ভেঙে গেলেও ছেলের জন্য খুব ভেঙে পড়েছিলেন। সে সময় তিনি অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন, চিকিৎসকদের চেষ্টায় সে যাত্রা বেঁচে যান। এরপর তিনি অসিত গুপ্তকে বিয়ে করেন ১৯৬৫ সালে, কিন্তু সেই সংসারও ১৯৭৬ সালে ভেঙে যায়।
হাজার চুরাশির মা লিখেছিলাম সেই সময়ে। উপন্যাসটা পড়লে বোঝা যাবে। ওই সময় তিনি অসম্ভব ঘুরে বেড়াতেন—তার একমাত্র কারণ ছিল মনের একটা কষ্টকে চাপতে চেষ্টা করা। হয়তো এটাই তাঁর জীবনের একটা টার্নিং পয়েন্ট বলে তিনি মনে করতেন।
তাঁর কোথায়, এদিকে আমি কোয়ালিটি রাইটিং-এর দিকে মন দিলাম অন্যদিকে আদিবাসীদের মধ্যে কাজ শুরু করলাম। এই দিকটা অবশ্যই আমার লেখাকে সমৃদ্ধ করতে শুরু করেছিল। একটা না দেখা ওয়ার্ল্ড, কেউ জানে না, বোঝে না—তার সমস্ত অনুভূতিগুলি ক্ষোভ-দুঃখগুলি আমার লেখার সঙ্গে খুব মিশে যাচ্ছিল।
এরপর তিনি ষাটের দশকের মাঝামাঝি এসে যে উপন্যাসগুলো লিখেন, তাকে তাঁর দ্বিতীয় পর্বের সাহিত্যকর্ম বলা যেতে পারে। এ সময় তিনি আলোচিত কিছু উপন্যাস লিখেন। এগুলোর মধ্যে আঁধার মানিক (১৯৬৬), কবি বন্দ্যঘটি গাঞির জীবন ও মৃত্যু (১৯৬৬), হাজার চুরাশির মা (১৯৭৪) উল্লেখযোগ্য।
মহাশ্বেতা দেবী দীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটিয়ে দিয়েছেন যে জনমানুষের সাথে, তাদের বড় একটি অংশ হলো আমাদের প্রান্তিক দলিত জনগোষ্ঠীর গোত্রভুক্ত।
মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে রাজনীতি এসেছে পূর্ণ-অবয়বে, যেখানে তিনি রাজনৈতিক অন্ধকার দিকগুলোকেও উপন্যাসের শৈলীতে নিয়ে এসেছেন। ঘরে ফেরা (১৯৭৯) উপন্যাসটিও রাজনৈতিক অন্তুর্বিশ্লেষণের ভিন্ন প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁর ছোটগল্পেও এই ভাবধারা প্রকাশ ঘটেছে।
মহাশ্বেতা দেবী মনে করেন সাহিত্যে শুধু হৃদয়-গ্রাহ্যতা নয়, মস্তিষ্ক-গ্রাহ্যতাও চাই। তিনি আরও জানান পাঠক-সমালোচককে আজ এ কথা বুঝতে হবে যে আমি যা-যা লিখেছি তার মধ্য দিয়ে এটাই বলতে চেয়েছি যে, যা-যা ঘটেছে তা শুধু আজই ঘটছে না, চিরকালই ঘটে আসছে। তাঁর মতে লেখকের কাজ হলো ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সেই ঘটনাবলিকে স্থাপন করা। তিনি প্রায়শ যে কথাটি বলে থাকেন তা হলো—তিনি ইতিহাসের প্রতি দায়বদ্ধ।
তিনি প্রান্তিক কণ্ঠস্বরকে তুলে এনেছেন মূলস্রোতের মানুষের সাহিত্যে। যা নিচের দিক থেকে ইতিহাসকে দেখবার ইঙ্গিত বহন করে, ওপরের দিক থেকে নয়। যা সাব-অলটার্ন স্ট্যাডিজের অংশ হয়ে দেখা দেয়। মার্ক্সবাদে সাব-অলটার্ন শব্দটির ব্যবহার পুরনো। আন্তেনিও গ্রামশির (১৮৯১-১৯৩৭) তাঁর বিখ্যাত কারাগারের নোটবুক বইটিতে এ সম্পর্কিত আলোচনার অবতারণা করেন। গ্রামশির মতে, কৃষকদের পক্ষে কলম ধরতে হবে বুদ্ধিজীবীদের।
পাহাড়ি অরণ্য-জীবনের সাথে ফুটে ওঠে পরিবেশের বিপন্নতার চিত্র, যা আজকের পৃথিবীকেও বিচলিত করে, সেই আখ্যান সাহিত্যে রূপ দিয়ে আদিবাসী জীবনে ঘটে যাওয়া উলগুলান (১৯০০), কোলহান (১৮৩৫) এবং হুল (১৮৫৫-৫৬)-কে নিয়ে আসেন। একের পর এক আদিবাসীদের জীবনকে নিয়ে এলেন উপন্যাসে। তাঁর আদিবাসী জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য: কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু (১৯৬৭), অরণ্যের অধিকার (১৯৭৫), চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তির (১৯৮০), সুরজ গাগরাই (১৯৮৩), টেরোড্যাকটিল, পূরণসহায় ও পিরথা (১৯৮৭), ক্ষুধা (১৯৯২) এবং কৈর্বত খণ্ড (১৯৯৪)। উল্লিখিত উপন্যাসগুলো ছাড়াও আরও বেশকিছু উপন্যাসে মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী প্রসঙ্গ এনেছেন, তবে তা বিচ্ছিন্নভাবে।
মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসীদের জীবন উপজীব্য করে প্রচুর ছোটগল্প রচনা করেন, এসব গল্পগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—শালগিরার ডাকে (১৯৮২), ইটের পরে ইট (১৯৮২), হরিরাম মাহাতো (১৯৮২), সিধু কানুর ডাকে (১৯৮৫) প্রভৃতি। এই সব গল্প-উপন্যাসে তিনি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সামরিক নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে যেমন আদিবাসী প্রতিবাদী চরিত্র চিত্রিত করেছেন। তেমনি এ দেশীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার শোষণের প্রতি প্রতিবাদ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর তুলে ধরেছেন।
মহাশ্বেতা দেবীর বিশিষ্টতা এই যে তিনি বাংলা সাহিত্যে সর্বাধিক আদিবাসী জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাস রচনা করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। জীবনকেন্দ্রিক উপন্যাসের ইতিহাস থেকে চরিত্র নির্মাণ করেছেন। আদিবাসী সংগ্রামের এবং ভারতীয় সংগ্রামের ইতিহাস থেকে বিপ্লবী এবং বীরের চরিত্র নিয়ে আসেন। যা বাংলা সাহিত্যের সংগ্রামী চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা সৃষ্টি করে।
তিনি যেমন ইতিহাস থেকে চরিত্র নিয়ে উপন্যাস রচনা করেন, তেমনি তাঁর রচিত উপন্যাসের চরিত্ররা যেন ইতিহাস হয়ে যায়। এক্ষেত্রে শুরুতেই আমরা স্মরণ করতে পারি অরণ্যের অধিকার উপন্যাসটির কথা। এই উপন্যাসের নায়ক বীরসা মুণ্ডাকে মহাশ্বেতা দেবী এনেছেন ভারতীয় দলিত সংগ্রামের ইতিহাস থেকে। এক্ষেত্রে মহাশ্বেতা দেবী নিজেই গ্রন্থটির ভূমিকায় বলেছেন— এই উপন্যাস রচনায় সুরেশ সিং রচিত ‘Dust storm and Hanging mist’ বইটির কাছে আমি সবিশেষ ঋণী। সুলিখিত তথ্যপূর্ণ গ্রন্থটি ছাড়া বর্তমান উপন্যাস রচনা সম্ভব হতো না।
ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে দলিত মানুষের স্থান দেননি ভারতীয় সরকার এমনকি ইতিহাসবীদরা। সেই কারণেই তিনি মুণ্ডা বিদ্রোহ নিয়ে আসেন স্বাধীন ভারতে এবং লেখেন চোট্টি মুণ্ডা ও তার তীর নামের উপন্যাস। তাই বীরসার কথা সবাইকে জানাতে চান তিনি। অরণ্যের আদিবাসী মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামকে অরণ্যের জীবনের সাথে এক করে, প্রকৃতি-মানুষ-জীবন সংগ্রামের পরম্পরা রচনা করেন, দেশীয় চেতনার উন্মেষ মেখে।
বীরসার চরিত্রটি যেমন ইতিহাসে ঘটে যাওয়া সত্যি ঘটনা নিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনি সুরজ গাগরাই উপন্যাসটির চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও তিনি সত্যি ঘটনা অবলম্বনে চরিত্র তৈরী করেছেন। এ বিষয়ে তিনি নিজেই বলেছেন—
সুরজ গাগরাই অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। সুবর্ণরেখা নদী বাঁধ প্রকল্প সত্যি, ব্যাপক আদিবাসী মালিকানা জমি অধিগ্রহণ সত্যি। ওই বড় প্রকল্পের অঙ্গ খড়কাই নদী বাঁধ প্রকল্প। খড়কাই বাঁধ সংঘর্ষ সত্যি, তা ১৯৮২/১৯৮৩ তে ঘটে। ওই সংঘর্ষের নেতা ছিলেন চাইবাসার কাছাকাছি ইলিয়াগড় নিবাসী গঙ্গারাম কালুরিয়া। তিনি সেনাবিভাগে ছিলেন। শর্ট সার্ভিস কমিশন-এর পর, অথবা ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন।
অতএব দেখা যাচ্ছে যে ১৯৮২-৮৩-তে ঘটে যাওয়া সুবর্ণরেখা বাঁধ প্রকল্প বিরোধী নেতা গঙ্গারাম কালুরিয়া-ই মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসের নায়ক হয়ে যান সুরজ গাগরাই নামে। শুধু বীরসা মুণ্ডা আর সুরজ গাগরাই চরিত্রটিই নয় মহাশ্বেতা দেবীর ক্ষুধা উপন্যাসটির চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সত্যি ঘটে যাওয়া সত্যি ঘটনা থেকে চরিত্র নিতে দেখা যায়। তিনি ক্ষুধা উপন্যাস লেখা প্রসঙ্গে বলেন—
আশির দশকে বিহারের তরুণ সাংবাদিকরা ‘মানাতুর মানুষখেকো’ লিখে পাঠক ও প্রশাসনকে কাঁপিয়ে দেয়। মানাতুর জমিদার, (নামটা লিখব না) মৌয়ার… সিং তাঁর নিজস্ব চিড়িয়াখানায়, খাঁচায় বন্দি চিতাবাঘকে, তাঁর বনডেড লেবার বা ভূমিদাদের মাংস মাঝে মাঝে খাওয়াতেন।… ঘটনা সত্যি। একটি নতুন মা ও তার শিশুকে বাঘের খাঁচায় ছুড়ে ফেলার ঘটনা যে সত্যি তা মালিকেরা বা ভূমিদাসরাই বলে।… ডালটনগঞ্জে যে সংবাদিকের ঘরে থাকতাম সে ঘর, ওই শিবাজী ময়দান, গান্ধী হল, পালামৌয়ের পথ ঘাট, সেদিনের তরুণ বুদ্ধিজীবী সহসাথীরা জানে ‘ক্ষুধা’ ও প্রতিটি অক্ষর সত্যি।
অর্থাৎ কৌয়ার, তেতরি ভূঁইন ও কসিলা চরিত্রগুলোও তিনি বাস্তব ঘটনা থেকে নিয়েছিলেন। তাই বলা যায় ঘটে যাওয়া ঘটনা যেমন ইতিহাস, তেমনি সেই ইতিহাস থেকে সংগৃহীত চরিত্রগুলো নিয়ে মহাশ্বেতার রচিত উপন্যাসও আর এক ইতিহাস হয়ে যায়।
আদিবাসী-উন্নয়নের কাজে এবং ভিন্ন ধরনের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নে মহাশ্বেতা দেবী যে প্রভূত সময় ব্যয় করেন, তাতে তাঁর লেখালেখির কাজে অনেক সময় ব্যাঘাত ঘটে। তাতে কি সামগ্রিকভাবে বাংলা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না? এই প্রশ্নের উত্তরে মহাশ্বেতার স্পষ্ট জবাব—
বাংলা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হলো কি না হলো, তা আমার বয়েই গেল। তার জন্য আমি কিছুমাত্র ভাবিত নই। আমার জীবিতকালে চেষ্টার দ্বারা যদি যাবজ্জীবন জেলে-থাকা বন্দীদের মুক্ত করতে পারি, অঞ্জলি সরকার যে কেরালায় বন্দী ছিল যদি তাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়, যদি আদিবাসী-সমাজের সেবায় আমি এইভাবে জীবন কাটাতে পারি তাতে আমার সাহিত্যের ক্ষতি হলেও আমার কিছু এসে যায় না। কারণ মানুষের জন্য কাজ না করে আমার উপায় নেই। প্রত্যেক মানুষেরই উচিত কর্মময়তার মধ্যে থাকা। মানুষের জন্যে কিছু যে না করে সে খুব ছোট হয়ে যায়। শুধু নিজের জন্য বাঁচার কোনো মানে হয় না।