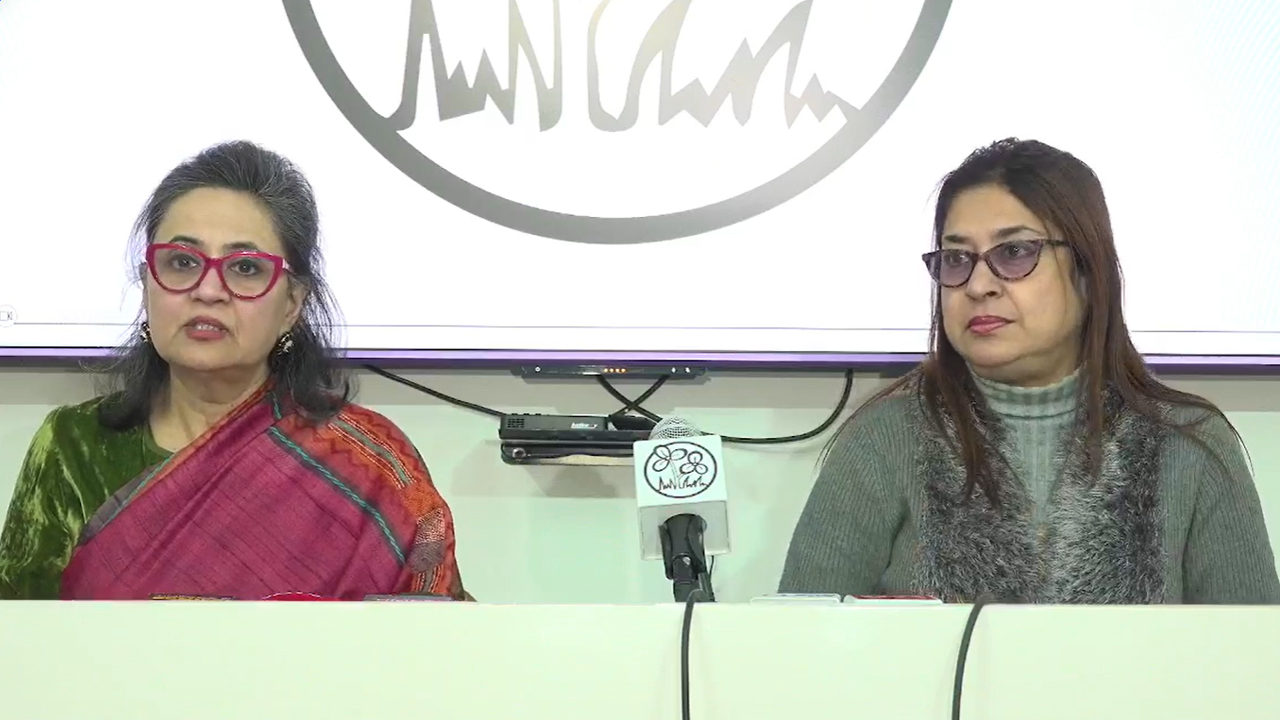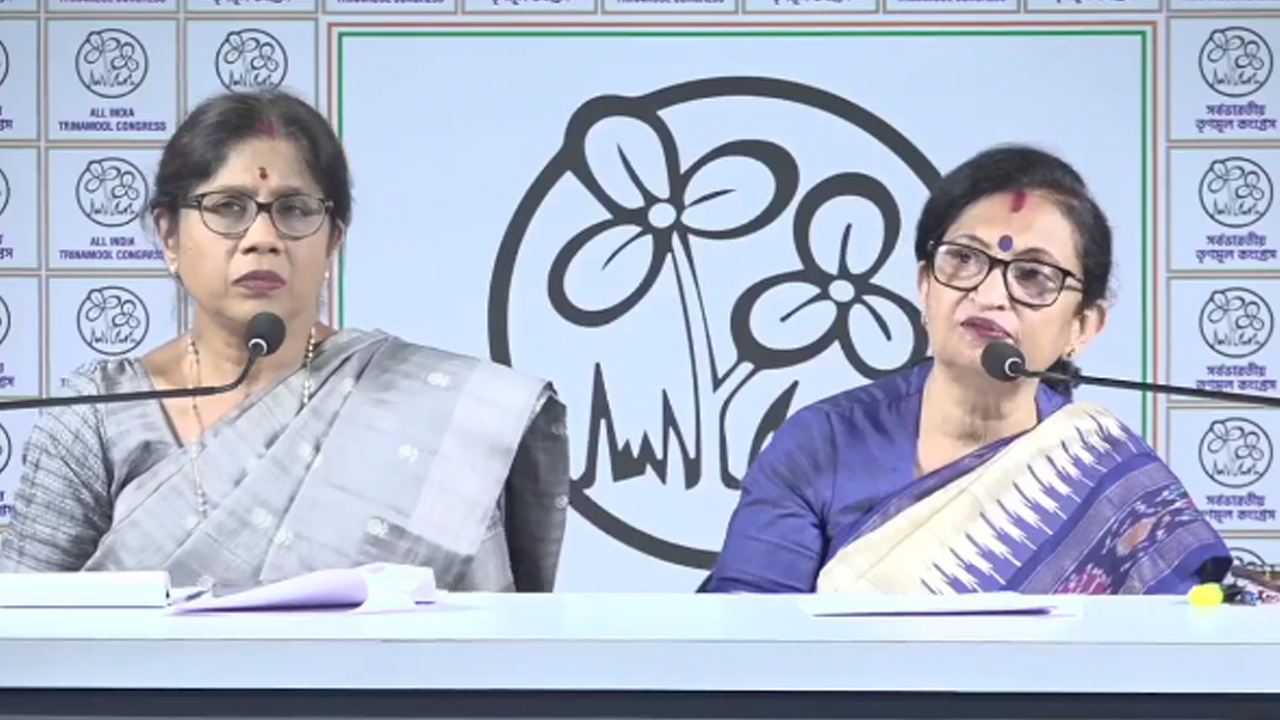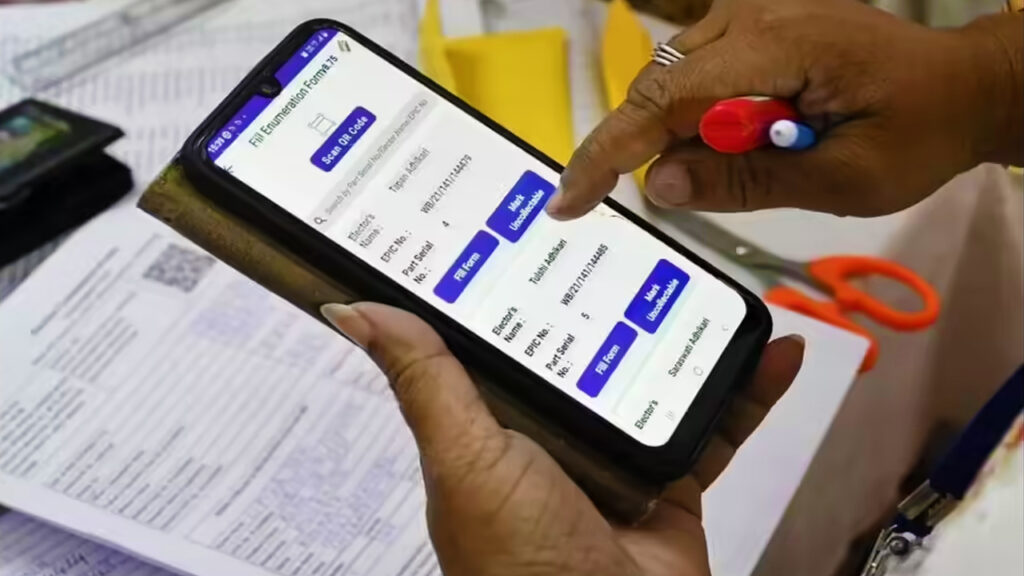রবীন্দ্র ভাবনায় জাতীয়তাবাদ
রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আধুনিক ভারতের অন্যতম স্থপতি। ইউরোপীয় রেনেসাঁ থেকে মানুষের মুক্তি, সমতা, স্বাধীনতা- এমন অনেক ধারণা গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এজন্য ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ভক্তির সীমা ছিল না। সেই ইউরোপীয় রেনেসাঁ এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা।
রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আধুনিক ভারতের অন্যতম স্থপতি। ইউরোপীয় রেনেসাঁ থেকে মানুষের মুক্তি, সমতা, স্বাধীনতা- এমন অনেক ধারণা গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এজন্য ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ভক্তির সীমা ছিল না। সেই ইউরোপীয় রেনেসাঁ এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা।
রবীন্দ্রনাথ নিজের জাতীয়তাবাদ নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, তিনি তাঁর জাতীয়তাবাদী ভাবনায় সমগ্র ভারতবাসীকে উজ্জীবিত করেছেন এবং আজও করছেন। তবে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদী যেমন সত্য, একই সঙ্গে তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদীও, যাকে বলে বিশ্বমানব। তবে তিনি উগ্র জাতীয়তাবাদকে প্রশ্রয় দেননি। কারণ, এর ভয়াবহতা তিনি জানতেন।
হিটলার, মুসোলিনি ছিলেন উগ্র জাতীয়তাবাদী। তাদের উগ্র জাতীয়তাবাদের পরিণতি কী, রবীন্দ্রনাথ তা প্রত্যক্ষ করেছেন। আমরাও সেটা কমবেশী জানি। রবীন্দ্রনাথ এক জাতিসত্তার সঙ্গে আরেক জাতিসত্তার অস্তিত্বের বহুমাত্রিক রূপ পরিগ্রহ করেছেন, একটি সহজ যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেছেন। প্রত্যক্ষ করেছেন সর্বব্যাপী দৃষ্টি দিয়ে।
তিনি একক নেশন বা জাতির ওপর আস্থা রাখেননি। সমাজে নানা রকম বিভক্তি বিদ্যমান থাকায় নেশন নির্মাণ সম্ভব নয়- এটাই ছিল তার অনাস্থার মূল কারণ। ন্যাশনালিজমের নাম দিয়েছেন তিনি ‘জিওগ্রাফিক্যাল ডেমন’। প্রথমদিকে তার ধারণা ছিল, ‘নেশন একটি মানস পদার্থ।’ কিন্তু পরে নেশনকে একটি অস্বাভাবিক অবস্থা হিসেবে দেখেছেন, যা জনগণকে ‘যান্ত্রিক প্রয়োজনে’ সংঘবদ্ধ করে।
তার ব্যাখ্যা, ভারতবর্ষে ন্যাশনালিজম খাটবে না। কারণ, ইউরোপে শাসক-শোষিতের যে ভেদ ঘটেছিল, সেটা জাতিগত বিভেদ নয়; শ্রেণীগত ভেদ। কিন্তু ভারতবর্ষে ভেদ ধর্ম ও জাতির নামে। তার মতে, দুর্বল ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে জাতি গঠনের চেষ্টা এসব ভেদবুদ্ধিকে আরো বাড়িয়ে দেবে।
কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের ভাবনাকে ‘উত্তর-আধুনিক’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। কারো কারো মতে, রবীন্দ্রনাথের নেশনবিরোধী সমালোচনায় স্টেটবিরোধী মতাদর্শ থাকলেও সেখানে স্বদেশপ্রেমের জায়গা আছে, কিন্তু ন্যাশনালিজমের নেই। রবীন্দ্রনাথ কড়া ভাষায় নেশনের সমালোচনা করেছেন, কিন্তু ততটা কড়াভাবে নো-নেশনের ছবি আঁকেননি। তিনি ঐক্যের প্রয়োজনে ভারতবর্ষে এক-রাষ্ট্রীয় শাসনের পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের পক্ষে মত দিয়েছেন। তিনি নো-নেশন সমাজে জনগণের উদ্ভাবনী শক্তির ওপর জোর দিয়ে বলেছেন, চীন, জাপান, ইরান, তুরস্ক প্রভৃতি এ ধরনের রাষ্ট্র।

আমলাতন্ত্রেরও কঠোর সমালোচনা করেছেন তিনি। তবে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় ‘যৌথতার নতুন নির্মাণের’ স্তুতি করলেও মানব চরিত্রের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার রীতিও তিনি মানতে চাননি। তিনি সেই রাষ্ট্রকে মানেননি, যে রাষ্ট্র স্বৈরাচার। স্বৈরাচারী সমাজের বিরুদ্ধেও তার ধিক্কার ছিল স্পষ্ট। ব্রিটিশ যুগে রাষ্ট্র ছিল স্বৈরাচার। রবীন্দ্রনাথ তাই চেয়েছিলেন সমাজকে আলাদা করে নেবেন রাষ্ট্রের সর্বভুক ও বুভুক্ষুগ্রাস থেকে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সমাজই প্রধান; রাষ্ট্র নয়। এ কথা তিনি বার বার বলেছেন, খুব জোর দিয়েই।
স্বৈরাচারী রাষ্ট্রশক্তি অমর নয়; তার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী- এই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ কখনো হারাননি। সেজন্যই তার তাসের দেশের তাসেরা মানুষ হয়ে ওঠে, অচলায়তন ভেঙে পড়ে, মুক্তধারা বইতে থাকে এবং রক্তকরবীর সেই ভীষণ রাজারও পতন ঘটে। রবীন্দ্রনাথের ‘সভ্যতার সংকট’-এ ইংরেজ রাজত্বের অবসানের অবশ্যম্ভাবিতার যে বিশ্বাস ফুটে উঠেছে, তার সেই একই বিশ্বাস সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রেও। তার পাহাড় মেঘ হয়, নদী থাকে সতত প্রবহমান, আর মানুষ এগিয়ে চলে মুক্তির লক্ষ্যে- সব বন্ধন ছিন্ন করে। তার মতে, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। মানুষের শক্তির ওপর আস্থা তার অবিচল।
তাই তিনি মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করেননি। জাতি, ধর্ম, বর্ণ কিংবা বিশেষ কোনো সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দেননি। রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদে কোনো বিশেষ মতাদর্শকেও শ্রেষ্ঠত্ব দেননি। তার জাতীয়তাবাদ উঠে এসেছে মানবিক চেতনা থেকে, আত্মোপলব্ধি থেকে।
প্রশাসনিক সুবিধার্থে ব্রিটিশ সরকার যখন বৃহত্তর বঙ্গকে দুই ভাগ করে পূর্ব বাংলা ও আসামকে একটি প্রদেশের মর্যাদা দিয়ে ঢাকাকে রাজধানী করে তখন তিনি বঙ্গভঙ্গ রদ করার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে বিভিন্ন সমাবেশ করেন। বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখালিখি শুরু করেন। তিনি পথে নেমে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রাখি বন্ধন করেন ও রচনা করেন বাংলার মাটি বাংলার জল।
১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ কৃষি-অর্থনীতিবিদ লিওনার্দ কে এলমহাস্টের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের নিকটবর্তী সুরুল গ্রামে ‘পল্লী পুনর্নির্মাণ সংস্থা’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ পরে এর নাম পরিবর্তন করে রেখেছিলেন ‘শ্রীনিকেতন’। এই শ্রীনিকেতনের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত স্বরাজ আন্দোলনের একটি বিকল্প ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের বিদ্বান ও পন্ডিতদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে সেখানে গ্রামের মানুষদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদানের বন্দোবস্ত করেন এবং তাদের মধ্যে বিশুদ্ধ জ্ঞান বিকাশের প্রয়াস নেন।
ত্রিশের দশকে তিনি ভারতবর্ষের অস্বাভাবিক বর্ণবিভেদ এবং বর্ণে বর্ণে ধরাছোঁয়ার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত মতামত প্রচার শুরু করেন। তিনি এই বর্ণবিভেদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা, কবিতা রচনা, বর্ণবাদীদের বিরুদ্ধে নাটক রচনা এবং কেরালার একটি মন্দিরে এই প্রথা ত্যাগের আহ্বান জানানোর মাধ্যমে তার আন্দোলন পরিচালনা করেন। মূলত দলিতদের সাধারণ সমাজে অবাধ প্রবেশাধিকারের সুযোগ করে দেওয়াই ছিল তার লক্ষ্য।
জীবনের শেষ দশকের পুরোটা রবীন্দ্রনাথ জনসমক্ষে ছিলেন। তার জনপ্রিয়তা এই সময়ে ছিল তুঙ্গে। ১৯৩৪ সালের ১৫ জানুয়ারি ভারতের বিহার রাজ্যে সংঘটিত প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী মন্তব্য করেছিলেন, এটা দলিতদের বশীভূত করার জন্য ঈশ্বরের একটি প্রতিশোধ। রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্যের জন্য গান্ধীকে জনসমক্ষে তিরস্কার করেন। এছাড়া বঙ্গের আর্থ-সামাজিক অবস্থার অবনতি এবং কলকাতায় দারিদ্র্যের প্রভাবের কারণে তিনি বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন। ১০০ লাইনের একটি মিত্রাক্ষরবর্জিত কবিতায় তিনি তার এই বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটান।
রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ প্রান্তে ভারত রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। বিশেষ করে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের মতো সাধারণ সমস্যার ভারে ভারতকে জর্জরিত হতে দেখে এবং হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-সংঘর্ষ, তাতে রাজনৈতিক দলগুলোর বাড়াবাড়ি রকমের ইন্ধন ও উস্কানি দিতে দেখেও তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছেন।
রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর মাত্র ৬ বছর পর, ১৯৪৭ সালের আগস্টে ভারত বিভক্ত হলো। সেই সময় হিন্দু-মুসলিম ভয়াবহ দাঙ্গা হলো। তাতে রাজনীতিকদের উস্কানি ও ইন্ধন ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই নৃশংস ট্র্যাজেডি দেখেননি। দেখলে তিনি কী করতেন জানি না।